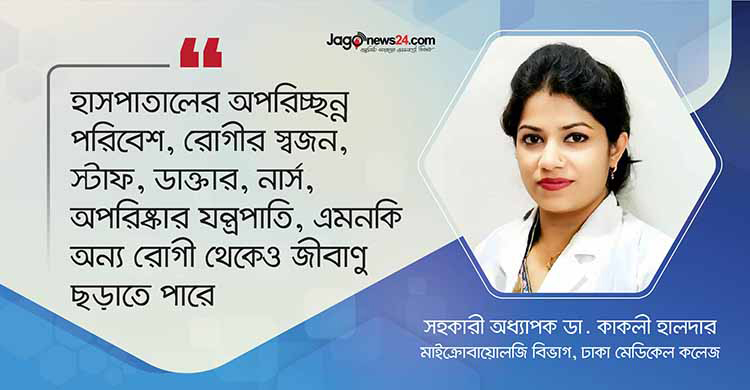কোনো দুর্ঘটনায় সুপারফিশিয়াল বা হালকা পুড়ে গেলে ব্যাথা অনেক বেশি হয়। কিন্ত ত্বকের গভীর পর্যন্ত নার্ভগুলো পুড়ে গেলে রোগীরা তুলনামূলক কম ব্যাথা অনুভব করেন। তবে অগ্নিদগ্ধ যেসব রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, তাদের বেশিরভাগের মৃত্যু হয় মূলত ক্ষতস্থানে ইনফেকশন বা জীবাণু সংক্রমণ হয়ে।
Advertisement
ইনফেকশন বা জীবাণু সংক্রমণ শুরু হয় পুড়ে যাওয়ার ২-১ দিন পর থেকে। এসময় রোগীরা যেসব রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় সেগুলো সাধারণত হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, রোগীর স্বজন, স্টাফ, ডাক্তার, নার্স, অপরিষ্কার যন্ত্রপাতি, এমনকি অন্য রোগী থেকেও ছড়াতে পারে।
আগুনে পুড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নানা বিষয় নিয়ে জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. কাকলী হালদার–
পুড়ে যাওয়া রোগীর সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। তাই এই রোগীর যত্নে দ্রুত এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে এর সঙ্গে হাসপাতালে দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা পর্যন্ত অনেক বিষয় জড়িত থাকে।
Advertisement
আগুনে পুড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন হবে?
>> দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিন। কাপড়ে আগুন লেগে গিয়ে থাকলে তা দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করুন।
>> পোড়া স্থানে ২০-৩০ মিনিট ধরে সাধারণ তাপমাত্রার ঠান্ডা (তবে বরফ নয়) পানি ঢালুন। এটি ব্যথা কমাতে এবং টিস্যুর ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।
>> দ্রুত পোড়া স্থান বা কাছাকাছি থাকা সব অলংকার বা টাইট কাপড় সরিয়ে ফেলুন। কারণ চাপে পোড়া স্থান ফুলে যেতে পারে।
Advertisement
>> পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাপড় বা গজ দিয়ে আলতো করে পোড়া স্থান ঢেকে দিন। পোড়া চামড়ার সঙ্গে লেগে যায় এমন কিছু ব্যবহার করা যাবে না।
>> চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথার ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।
>> সম্ভব হলে পোড়া অঙ্গকে হার্টের লেভেলের চেয়ে উঁচুতে রাখুন, এতে ফোলা কম হবে।
>> গুরুতর পোড়া হলে দ্রুত রোগীকে বার্ন ইউনিটে বা নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান।
জীবাণু সংক্রমণ কেন হয়?
>> পোড়া রোগীদের শরীরে সংক্রমণের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে। ত্বক আমাদের শরীরের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর। ত্বক পুড়ে গেলে এই স্তরটি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক) সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
>> তীব্র পোড়ার কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, যা সংক্রমণকে আরও সহজ করে তোলে।
>> অনেক বেশি পুড়ে গেলে শরীর থেকে প্রচুর তরল এবং প্রোটিন বের হয়ে যায় যা জীবাণু সংক্রমণ তরান্বিত করে।
>> পোড়া ক্ষতস্থান জীবাণু প্রবেশের জন্য একটি খোলা দরজা হিসেবে কাজ করে।
যে ধরনের সংক্রমণ দেখা যায়
১. ক্ষতস্থান সংক্রমণ: পোড়া স্থানেই ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
২. সেপসিস: ক্ষত থেকে সংক্রমণ রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়লে সেপসিস হয় যা অত্যন্ত গুরুতর এবং মৃত্যুঝুঁকির কারণ।
৩. নিউমোনিয়া: গরম ধোঁয়ায় শ্বাসনালী পুড়ে গেলে বা রোগী দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেটরে থাকলে জীবাণু আক্রান্ত হয়ে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
৪. মূত্রনালীর সংক্রমণ: দীর্ঘদিন মূত্রনালীর ক্যাথেটার ব্যবহার করতে হলে এই সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
কীভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়?পোড়া রোগীদের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়-
১. হাত ধোয়া: স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীর সংস্পর্শে আসা সকলকেই নিয়মিত হাত ধুতে হবে। রোগীকে ও রোগীর বিছানা বা আশেপাশে স্পর্শ করার আগে পরে এবং রোগীর শরীরের কোন তরল স্পর্শ করলে অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধুতে হবে।
২. ভিজিটর নিয়ন্ত্রণ: দর্শনার্থী প্রবেশ না কমাতে পারলে ইনফেকশনের সংখ্যা কমানো সম্ভব না। তাই হাসপাতাল কতৃপক্ষকে ভিজিটর কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যাবস্থা নিতে হবে।
৩. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম: চিকিৎসক ও নার্সদের অবশ্যই গ্লাভস, গাউন, মাস্ক এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
৪. জীবাণুমুক্ত পরিবেশ: বার্ন ইউনিট বা হাসপাতালের পরিবেশকে যথাসম্ভব জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুনাশক (০.৫% হাইপোক্লোরাইট সলিউশন, ৭০% অ্যালকোহল, ক্লোরহেক্সিডিন ইত্যাদি) ব্যবহার নিশিত করতে হবে।
৫. রোগীকে আলাদা রাখা: সংক্রমিত রোগীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখতে হবে যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।
৬. ক্ষত ড্রেসিং: ড্রেসিং পরিবর্তন করার সময় জীবাণুমুক্ত কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
৭. পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ: বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং হাসপাতালের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
৮. নিয়মিত পরীক্ষা: নিয়মিত রোগীর ক্ষত থেকে নমুনা নিয়ে জীবাণুর উপস্থিতি এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে।
আগুনে পোড়া রোগীর মৃত্যুর প্রধান কারণ কী?
>> শ্বাসতন্ত্র পুড়ে যাওয়া: আগুনে পুড়ে গেলে শ্বাসনালী পুড়ে যেতে পারে এবং ধোঁয়ার কারণে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটা মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। এটা সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাসকে ব্যাহত করে এবং ফুসফুসে দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়।
>> সেপসিস: মারাত্মক সংক্রমণ রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়লে সেপসিস হয়, যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয় এবং শক তৈরি করে।
>> শক: পোড়ার ফলে শরীর থেকে অত্যাধিক তরল হারানোর কারণে রক্তচাপ কমে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছায় না। ফলে শক হয়। এটি পোড়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।
>> অর্গান ফেইলিউর: সংক্রমণ বা শকের কারণে কিডনি, লিভার, হার্ট এবং ফুসফুসের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে।
>> হাইপোথার্মিয়া: শরীরের বিশাল অংশ পুড়ে গেলে ত্বকের অনুপস্থিতিতে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। ফলে শরীরের তাপমাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে পারে।
>> ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি: রোগীর এবং রোগীর স্বজনদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাও জরুরি।
এত সব জটিলতার পরেও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মেডিকেল পেশাজীবীদের পরিশ্রমে অনেক রোগীই সেরে ওঠেন। তবে সেই সঙ্গে রোগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং তরল গ্রহণ করতে হবে। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় এবং দ্রুত নিরাময়ে সাহায্য করে। কিছু ক্ষেত্রে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে নির্দিষ্ট কিছু ভ্যাকসিনের সুপারিশ করা হয়ে থাকে।
পোড়া রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ছোট একটি ভুলও গুরুতর জটিলতা তৈরি করতে পারে। তাই সবসময় দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা উচিত।
এএমপি/এএসএম