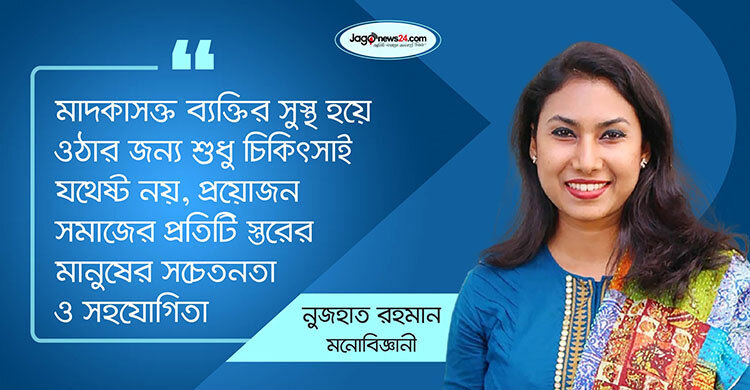মাদকাসক্ত মানেই কি অপরাধী? সমাজের চোখে যেন একরকম ঠাঁই-ঘৃণা, উপেক্ষা আর একঘরে করে রাখা। অথচ এই মানুষগুলো কারও না কারও হারিয়ে ফেলা স্বজন, ছিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের গল্প। তারা কি শুধুই শাস্তির যোগ্য, নাকি দরকার চিকিৎসা আর সহমর্মিতার ছায়া? এ ধরনের নানান বিষয় নিয়ে মনোবিজ্ঞানী নুজহাত রহমানের সঙ্গে কথা বলেছে জাগো নিউজ। নুজহাত রহমানের মতে, মাদকাসক্তি কোনো খারাপ অভ্যাস নয়, এটা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একটি জটিল অবস্থা। তাই সমাজের ভাবনায় বদল আনা জরুরি। শাস্তি নয়, চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এগিয়ে আসা দরকার।
Advertisement
নুজহাত রহমানের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাগো নিউজের সহ-সম্পাদক জান্নাত শ্রাবণী।
জাগো নিউজ: আপনার অভিজ্ঞতায় একজন মানুষ সাধারণত কী কারণে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন? এর পেছনে মানসিক বা সামাজিক কোন কারণগুলো কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?
নুজহাত রহমান: একজন মানুষের মাদকে আসক্ত হওয়ার পেছনে নানান ধরনের কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা, পারিবারিক অশান্তি; বিশেষ করে বাবা-মায়ের বিবাদ বা ‘ব্রোকেন ফ্যামিলি’র প্রেক্ষাপট থেকেও একজন ব্যক্তি মাদকে জড়িয়ে পড়তে পারেন।
Advertisement
যেসব পরিবারে সম্পর্কের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা থাকে, সেসব পরিবারে বাস করা যে কেউ- সন্তান, মা বা বাবা মাদকে আসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। এই ব্যক্তিরা অনেক সময় মাদককে একটি ‘কোপিং মেকানিজম’ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। মানসিক চাপ বা হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তারা ভুল পথে পা বাড়ান, যেটা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা।
শুধু পারিবারিক বা মানসিক কারণ নয়, কৌতূহলও মাদকাসক্তির একটি বড় কারণ। অনেক সময় তরুণ-তরুণীরা বন্ধুবান্ধবের খপ্পরে পড়ে মাদক গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ‘একবার খেলে কী হয় দেখে নেই’-এই মানসিকতা থেকেই অনেকে মাদকের জগতে ঢুকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়ে।
সিগারেট অনেক সময় মাদকে আসক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে আরও ক্ষতিকর মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকে। শুধু মাদক নয়, এর পাশাপাশি গেমস, পর্নোগ্রাফি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত আসক্তিও একই ধরনের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।
আরও পড়ুন বন্ধু যদি নেশায় জড়ায় স্মার্টফোন না থাকলেই দমবন্ধ লাগে? জেনে নিন ভয়টির নাম ও প্রতিকারজাগো নিউজ: মাদকাসক্তি কি শুধুই খারাপ অভ্যাস, নাকি এটি একটি রোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত?
Advertisement
নুজহাত রহমান: মাদক গ্রহণকে অনেকেই শুধুই খারাপ অভ্যাস বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এতটা সহজ নয়। একজন মানুষ যখন প্রথম মাদক ব্যবহার শুরু করেন, তখনই তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন না। সাধারণত কৌতূহল থেকে প্রথমে কেউ মাদক গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে হয়তো একবার মাদক গ্রহণের মাধ্যমে সে আনন্দ বা উত্তেজনা অনুভব করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই পরিমাণ মাদক আর তাকে সেই আনন্দ দিতে পারে না। তখন তাকে সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য মাদকের পরিমাণ বাড়াতে হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে সে মাদকের প্রতি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
শুধু পরিমাণই নয়, মাদক গ্রহণের ঘনত্ব বা ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ, আগে যে ব্যক্তি মাসে একবার নিত, সে সপ্তাহে একবার, পরে দিনে একবার এমনকি দিনে একাধিকবারও গ্রহণ করতে শুরু করে। এই ধাপে এসে তার ডিপেনডেন্সি বা নির্ভরতা তৈরি হয়। তখনই তাকে মাদকাসক্ত বলা যায়।
এটা বোঝা খুব জরুরি যে, মাদকাসক্তি শুধু খারাপ অভ্যাস নয়, এটি একটি মানসিক রোগ। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মানসিক রোগ নির্ণায়ক গ্রন্থ ডিএসএম (ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিজঅর্ডার্স) অনুযায়ী, মাদকাসক্তিকে একটি মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
মাদকাসক্তি একটি ক্রনিক রিল্যাপসিং ব্রেইন ডিজিজ, অর্থাৎ এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং বারবার ফিরে আসা মস্তিষ্কজনিত রোগ। এ রোগে মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যা একজন ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণকে প্রভাবিত করে। ফলে এর প্রভাব পড়ে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক- তিনটি দিকেই। এ কারণে মাদকাসক্তিকে একটি মনোদৈহিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর চিকিৎসাও সেই অনুযায়ী দিতে হয়।
সবচেয়ে আশার কথা, মাদকাসক্তির চিকিৎসা আছে। যথাযথ চিকিৎসা, কাউন্সেলিং এবং সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে একজন আসক্ত ব্যক্তি আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।
জাগো নিউজ: একজন আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রক্রিয়াটি কীভাবে পরিচালিত হয়? মানসিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং কতটা জরুরি এখানে?
নুজহাত রহমান: মাদকাসক্তির চিকিৎসা শুধু ওষুধে নির্ভরশীল নয়, এটি একটি বিস্তৃত ও সমন্বিত পদ্ধতি, যাকে বলা হয় বায়োসাইকোসোশ্যাল মডেল। এই মডেল অনুযায়ী একজন আসক্ত ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক তিনটি দিকেই সমানভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
প্রথমত, শারীরিক চিকিৎসার মাধ্যমে আসক্ত ব্যক্তির শরীর থেকে মাদকের প্রভাব দূর করা হয় এবং তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা হয়।
দ্বিতীয়ত, মানসিক চিকিৎসার অংশ হিসেবে মনোরোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট) ও সাইকোথেরাপিস্টরা কাজ করেন। তারা হতাশা, উদ্বেগ, মানসিক ট্রমা বা আচরণগত সমস্যাগুলোর চিকিৎসা দেন, যা অনেক সময় আসক্তির মূল কারণ হয়।
তৃতীয়ত, সামাজিক পুনর্বাসনের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসার একপর্যায়ে দেখা হয়, কীভাবে এই ব্যক্তি আবার সমাজে ফিরতে পারে, কর্মজীবনে যুক্ত হতে পারে, পরিবার ও সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে যারা যুক্ত থাকেন- চিকিৎসক, বিশেষ করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (সাইকিয়াট্রিস্ট), অ্যাডিকশন প্রফেশনাল, যারা নির্দিষ্টভাবে মাদকাসক্তদের নিয়ে কাজ করেন, সাইকোথেরাপিস্ট ও সার্টিফায়েড কাউন্সেলর, যারা মানসিক সহায়তা ও কাউন্সেলিং প্রদান করেন।
বিদেশে অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল ওয়ার্কার বা সামাজিক সহায়তাকর্মীরাও এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশে এখনো সোশ্যাল ওয়ার্ক পেশাটি কাঠামোগতভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে এখানে চিকিৎসকের পাশাপাশি সার্টিফায়েড কাউন্সেলর, অ্যাডিকশন প্রফেশনাল এবং সাইকোথেরাপিস্টরাই মূলত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজটি পরিচালনা করেন।
জাগো নিউজ: বাংলাদেশের মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলো কতটা মানসম্পন্ন বা কার্যকর?
নুজহাত রহমান: বাংলাদেশে বর্তমানে বেশকিছু মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তবে একটি নিরাময় কেন্দ্র সত্যিই মানসম্পন্ন কি না, তা বোঝার জন্য কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। কেউ যদি সেগুলো যাচাই করে দেখতে পারেন, তাহলে সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
যেসব বিষয় দেখে বুঝবেন কেন্দ্রটি মানসম্পন্ন- খেয়াল রাখতে হবে নিরাময় কেন্দ্রে একজন বা একাধিক কনসালট্যান্ট সাইকিয়াট্রিস্ট (মনোরোগ বিশেষজ্ঞ) নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছেন কি না। ২৪ ঘণ্টা ডিউটি ডাক্তার এবং সার্বক্ষণিক নার্স ও ওয়ার্ড বয় রয়েছে কি না। ট্রেইনিংপ্রাপ্ত নার্স ও সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে কি না, যারা মাদকাসক্তদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ। আরও খেয়াল রাখতে হবে মাদকাসক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় কি না, যাতে তারা বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে পুনরায় মাদক সংগ্রহ করতে না পারেন। কারণ চিকিৎসার শুরুতে রোগীদের মধ্যে মাদক ছাড়ার মানসিক-শারীরিক যন্ত্রণা দেখা দেয়, সেই সময় তাদের দায়িত্বশীল ও সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় কি না। এছাড়া নিয়মিত কাউন্সেলিং এবং অ্যাডিকশন প্রফেশনালদের মাধ্যমে মানসিক সহায়তা দেওয়া হয় কি না। চিকিৎসা পদ্ধতিতে বায়োসাইকোসোশ্যাল মডেলের সব দিক অন্তর্ভুক্ত আছে কি না? অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলো সমান গুরুত্ব পাচ্ছে কি না।
চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে নিরাময় কেন্দ্রটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে কি না। রোগীদের থাকার জায়গা আরামদায়ক এবং নিরাপদ কি না। রোগীদের জন্য বিনোদন বা খেলাধুলার সুযোগ, ব্যায়াম করার ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় কি না। ফ্রি টাইমে মানসিকভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে এমন সুযোগ থাকছে কি না। একই সঙ্গে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন আছে কি না এটি অবশ্যই যাচাই করা উচিত। কারণ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত এবং নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হয়।
জাগো নিউজ: পরিবার বা সমাজ কীভাবে একজন মাদকাসক্তকে সহযোগিতা করতে পারে?
নুজহাত রহমান: একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যখন চিকিৎসা গ্রহণ করেন, মাদক থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, তখন তার পাশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় পরিবার এবং সমাজের সহায়তা। কারণ, দীর্ঘদিন বা বহু বছর ধরে মাদকের সঙ্গে লড়তে থাকা একজন মানুষের জীবনে অনেক নেতিবাচক অভিজ্ঞতা জমে হয়। পরিবার-সমাজের কাছ থেকেও তিনি অনেকবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, অবহেলা ও অপমানের শিকার হয়েছেন। তাই পরিবার ও সমাজের উচিত তাকে শুধুই একজন ‘খারাপ অভ্যাসের মানুষ’ হিসেবে না দেখে একজন রোগী হিসেবে দেখা এবং উপলব্ধি করা যে মাদকাসক্তি একটি মানসিক ও শারীরিক রোগ। সে যদি মাদক থেকে মুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করে, তাহলে তার প্রতি পুরোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলাই উচিত।
পরিবার ও সমাজ যদি তাকে গ্রহণ না করে, যদি তার প্রতি বিরূপ আচরণ করে, তাহলে তার পুনরায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই ব্যক্তির মধ্যে তখন ফিরে আসার ইচ্ছেটাই হারিয়ে যেতে পারে। বরং সে যদি দেখে পরিবার তাকে আবার ভালোবাসা দিচ্ছে, সমাজের মানুষ তাকে সম্মান করছে, পুনরায় সমাজে জায়গা করে দিচ্ছে, তাহলে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। তখন সে নিজেকে মূল্যবান ভাবতে শেখে।
অনেক সময় একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি চিকিৎসার পরপরই হয়তো কোনো কাজ করতে পারেন না। হয়তো তার পড়াশোনা হয়নি, চাকরি বা ব্যবসাও নেই। তাই বলে তাকে অযোগ্য বা অপ্রয়োজনীয় ভাবা ঠিক নয়। কারণ, সে একজন মানুষ এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। সে পরিবারের সদস্য, সমাজের অংশ এ পরিচয়টিই তাকে শক্তি জোগায় নতুন করে শুরুর। এ কথাগুলো মুখে বললেই হয় না আচরণে বোঝাতে হয়, অনুভব করাতে হয়। তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলা, তাকে সম্মান দেওয়া, একটু সময় দেওয়া এসব ছোট ছোট আচরণের মাধ্যমেই বোঝানো সম্ভব যে, আমরা তাকে এখনো গ্রহণ করি। সে এখনো আমাদেরই একজন।
জাগো নিউজ: অনেকে মনে করেন, মাদকাসক্তদের শাস্তি দিলেই সমাজ রক্ষা পাবে। আপনার মতে এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা যৌক্তিক?
নুজহাত রহমান: ‘মাদকাসক্তদের শাস্তি দিলেই সমাজ রক্ষা পাবে’ এটি একটি ভুল ধারণা। কারণ, মাদকাসক্তি কোনো অপরাধ নয়, এটি একটি মানসিক ও শারীরিক রোগ। এ সমস্যার সমাধান শাস্তি দিয়ে নয়, বরং চিকিৎসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে। সমাজকে বুঝতে হবে, একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। যদি আমরা তাকে দোষারোপ না করে সাহায্য করতে এগিয়ে আসি, তাহলে তিনি নিজেই চিকিৎসা নিতে আগ্রহী হবেন। তাদের প্রতি যদি ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়, তাহলে তার সুস্থ হয়ে ওঠার পথ সহজ হবে।
একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি সময়মতো চিকিৎসা পান, পুনর্বাসন পান, তাহলে তিনিও হয়ে উঠতে পারেন সমাজের একজন উপকারী, সক্রিয় ও শক্তিশালী সদস্য। অন্যদিকে, যদি তাকে ঘৃণা করা হয়, সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় কিংবা শুধু শাস্তির পথ বেছে নেওয়া হয়, তাহলে সে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন সে সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই মাদকাসক্তদের প্রতি ঘৃণা নয়; সহানুভূতি, গ্রহণযোগ্যতা এবং চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।
জাগো নিউজ: পুলিশি ধরপাকড় বা জেল এসব কি একজন আসক্তের চিকিৎসায় সহায়ক নাকি আরও ক্ষতিকর হতে পারে?
নুজহাত রহমান: মাদকাসক্তির সমস্যার সমাধানে পুলিশি হস্তক্ষেপ সবসময় কার্যকর বা সহায়ক নয়। অবশ্যই বাংলাদেশের আইনে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে, যা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দায়িত্বের আওতায় পড়ে। কিন্তু একজন পেশাদার কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট হিসেবে আমার অভিমত মাদকাসক্তদের চিকিৎসার আওতায় আনা, তাদের সচেতন ও চিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করা-এটাই হওয়া উচিত পরিবার ও সমাজের প্রধান দায়িত্ব।
একজন মাদকাসক্তকে শুধু পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া কিংবা তাকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে শাস্তির মুখে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে তার সমস্যা সমাধান হয় না। বরং যে কোনোভাবে তাকে চিকিৎসার জন্য মোটিভেট করা, প্রয়োজনে বোঝানো এবং অবশেষে তাকে কোনো রিহাবিলিটেশন সেন্টারে পাঠানো-এটাই সবচেয়ে দায়িত্বশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিই শুধু মানবিক নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূও। কারণ মাদকাসক্তি একটি চিকিৎসাযোগ্য রোগ। এর সমাধানও চিকিৎসার মধ্য দিয়েই খুঁজতে হবে, শাস্তি দিয়ে নয়।
জাগো নিউজ: আপনার মতে, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় সমাজের কোন কোন স্তরের মানুষের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি দরকার?
নুজহাত রহমান: একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য শুধু চিকিৎসাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতা। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র সব জায়গায় তার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ অত্যন্ত জরুরি। পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মা বা অভিভাবকদের বুঝতে হবে, বকাঝকা বা কঠোর ব্যবহার নয় বরং সন্তানের অবস্থান বুঝে, তার অনুভূতির জায়গায় দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলাটাই বেশি ফলপ্রসূ।
মাদকাসক্ত ব্যক্তি অনেক সময় নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের ভেতরে অপরাধবোধ ও অনুশোচনা থাকে। তারা জানেন, তারা একটি ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এই অপরাধবোধের কথা তারা প্রকাশ করতে পারেন না। তাই তাদের আচরণে সেই অদৃশ্য কষ্টের জায়গাটা বুঝে সংবেদনশীলভাবে আচরণ করা দরকার।
সমাজের অন্য সদস্যদেরও বুঝে নেওয়া উচিত যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি কোনো খারাপ মানুষ নন, বরং তিনি একজন অসুস্থ মানুষ। তাই তাকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা, অনবরত উপদেশ দেওয়া অথবা অবহেলা করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বরং তাকে সহায়তা করতে হবে, যাতে তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেন। এ মানুষগুলোকে যদি আমরা বুঝতে পারি, তাদের বিচার না করি, তাদের একঘরে না করি, তাহলে তারাও সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার সাহস ও শক্তি পাবেন। কারণ, সহযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা মাদকাসক্তি থেকে উত্তরণের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
জাগো নিউজ: আপনার জন্য শুভ কামনা।নুজহাত রহমান: আপনাকে ধন্যবাদ।
জেএস/এমএফএ/জিকেএস